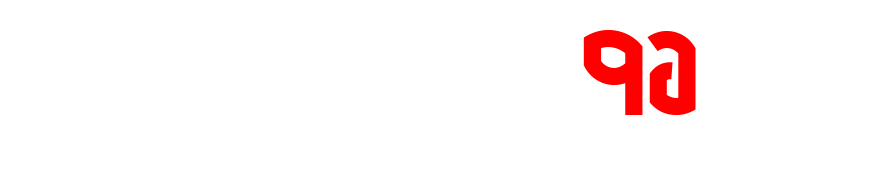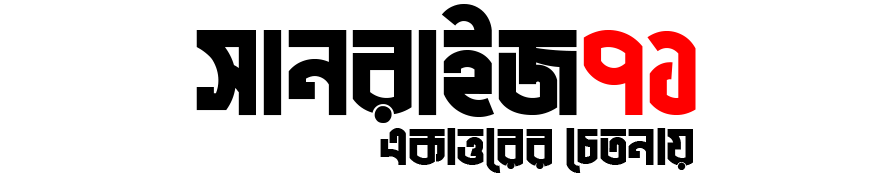বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প আজ এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) হিসেবে পাওয়া বিশেষ সুবিধা হারানোর পরিস্থিতিতে দেশীয় ওষুধ উৎপাদন খাতের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন শিল্প সংশ্লিষ্টরা। গতকাল শনিবার বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি ও বাংলাদেশ হেলথ রিপোর্টার্স ফোরাম (বিএইচআরএফ) আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় উঠে এসেছে আশঙ্কাজনক তথ্য— সরকারের উদাসীনতার কারণে দেশের ওষুধ শিল্প আবারও ৮০-এর দশকে ফিরে যেতে পারে।
কেন হুমকির মুখে ওষুধ শিল্প?
২০২৬ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ এলডিসি তালিকা থেকে উত্তরণের পর ট্রিপস (TRIPS) চুক্তির আওতায় মেধাস্বত্ব আইনের পূর্ণ প্রয়োগ শুরু হবে। এর ফলে, বর্তমানে বাংলাদেশ যে সুবিধা পেয়ে জীবনরক্ষাকারী ওষুধের জেনেরিক উৎপাদন করতে পারছে, তা বাধাগ্রস্ত হবে। বিশেষ করে, ২০২৪ সালের নভেম্বরের পর নতুন কোনো পেটেন্টেড ওষুধ উৎপাদনের অনুমতি পাওয়া কঠিন হবে।
এই সংকট মোকাবিলায় ঔষধ বিষয়ক সমিতি এক হাজারেরও বেশি নতুন ওষুধ উৎপাদনের অনুমোদন চেয়েছে। কিন্তু ড্রাগ কন্ট্রোল কমিটির (ডিসিসি) সভা অনুষ্ঠিত হলেও মাত্র ৩০০টি ওষুধ অনুমোদিত হয়েছে। বাকিগুলো অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়ে গেছে।
সময় ফুরিয়ে আসছে: মাত্র তিন মাস?
ঔষধ শিল্প সমিতির মহাসচিব ড. মো. জাকির হোসেন সতর্ক করে বলেন, “আমাদের হাতে সময় মাত্র তিন মাস। যদি এখনই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তাহলে দেশের মানুষকে চড়া মূল্যে বিদেশি ওষুধ কিনতে হবে, যা অনেকের নাগালের বাইরে চলে যাবে।”
তিনি আরও উল্লেখ করেন, আগে প্রতি দুই থেকে তিন মাসে ডিসিসি সভা হতো, কিন্তু এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতির। অথচ, এলডিসি উত্তরণের পর এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা জরুরি।
সরকারের সঙ্গে শিল্পের সংযোগহীনতা: প্রধান সমস্যা
শিল্প সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করেছেন, সরকার ওষুধ নীতিমালা প্রণয়নে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। সমিতির কোষাধ্যক্ষ মো. হালিমুজ্জামান বলেন, “আমরাও দেশের অংশ, আমাদের মতামত উপেক্ষা করা উচিত নয়। যদি এই অবস্থা চলতে থাকে, তাহলে দেশের ওষুধ শিল্প আমদানিনির্ভর হয়ে পড়বে এবং ৮০-এর দশকের মতো পিছিয়ে যাবে।”
১৯৮২ সালের ওষুধ নীতির সাফল্য ও বর্তমান চ্যালেঞ্জ
১৯৮২ সালের জাতীয় ওষুধ নীতি বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পকে গতিশীল করেছিল, যা আজ বিশ্বের ১৬০টি দেশে রফতানি হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান নীতিগত দুর্বলতা এই অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে পারে।
ঔষধ শিল্প সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি এম মোসাদ্দেক হোসেন বলেন, “মার্কিন শুল্কনীতির প্রভাব ওষুধ খাতে পড়বে না, কারণ এ খাতে কোনো ট্যারিফ নেই। কিন্তু সরকার যদি এখনই সঠিক নীতি না নেয়, তাহলে পুরো শিল্পই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।”
কী করা উচিত? জরুরি পদক্ষেপের আহ্বান
১. ডিসিসি সভা দ্রুত অনুষ্ঠান: অবিলম্বে বাকি ওষুধগুলোর অনুমোদন দেওয়া হোক।
২. শিল্পের সঙ্গে আলোচনা: ওষুধ নীতিতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সম্পৃক্ত করতে হবে।
৩. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা: এলডিসি উত্তরণের পর কীভাবে শিল্প টিকবে, তা নিয়ে এখনই ভাবতে হবে।
৪. স্থানীয় উৎপাদন বাড়ানো: জীবনরক্ষাকারী ওষুধের উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াতে বিনিয়োগ জরুরি।
উপসংহার: সময় নষ্ট করার সুযোগ নেই
বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প আজ এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। সরকার যদি এখনই জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে এই শিল্পের অগ্রগতি থমকে যাবে, যা দেশের স্বাস্থ্যখাতের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে। মাত্র তিন মাসের মধ্যে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া গেলে এই সংকট কাটানো সম্ভব।
আরও পড়ুন: বর্তমান ভাইরাল জ্বর: আতঙ্ক নয়, সচেতনতাই প্রতিরোধের চাবিকাঠি
#ওষুধশিল্প #ঔষধসমিতি #ট্রিপসচুক্তি #স্বাস্থ্যখাত #বাংলাদেশ